দেশ
তুর্কী শব্দ মূ-আয়নহ থেকে এসেছে ময়না ধর্মমঙ্গল থেকে মঙ্গলকাব্য সর্বত্র আছে ময়না

মধ্যযুগের বাংলার ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে ময়না একটি বিশিষ্ট নাম। গৌড় এবং ময়নার মধ্যে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত এই পথের বর্ণনা ধর্মমঙ্গলকার তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গীতে করেছেন। ধর্মমঙ্গলে কাব্যে যা লেখা আছে, তার প্রেক্ষিত ছিল পাল শাসনের রেশ। এই পথ যে তার আগে ছিল না, তার প্রমাণ ধর্মমঙ্গল দিতে পারে না। সম্ভবত গুপ্তযুগেও এই পথই ছিল রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাধারণ মানুষের চলাচলের পথ। অশোকের সময়েও তাম্রলিপ্ত যাতায়াতের জন্য এই পথ ব্যবহার হত। বর্তমানের সিংভূম জেলার পোড়াহাট অঞ্চলের তাম্রখনি থেকে ময়ুরভঞ্জের বামনঘাটি হয়ে এই সড়ক ধরে তাম্রলিপ্ততে তামার ব্যবসা চলত। সম্ভবত তামার ব্যবসায়ের জন্য এই বন্দর তাম্রলিপ্ত নামে পরিচিত ছিল। ময়না নামের উৎপত্তি নিয়ে কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যেমন, হাওড়া ডোমজুড় অঞ্চলে ‘ময়নার বিল’ একটি জায়গা আছে। হিন্দী ও মারাঠীতে ‘মৈনা’ শব্দের অর্থ ময়না। প্রাকৃত বা সংস্কৃত ভাষাতেও ময়না শব্দটি প্রচলিত। ময়না এক প্রকাস কাঁটা-ঝোপ।তুর্কীরা এই অঞ্চলকে মৃত দেখে ‘মূ-আয়নহ’ শব্দ ব্যবহার করতে পারেন।
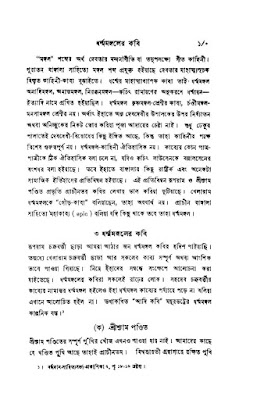
পরবর্তীকালে ধর্মমঙ্গল রচয়িতাগণ তাঁদের কাব্যে এই আরবী শব্দটি প্রয়োগ করে থাকতে পারেন। ময়না শব্দটি তিব্বতী কোন শব্দের অপভ্রংশও হতে পারে। ফরাসী পন্ডিতগণ একদা এই অঞ্চলে তিব্বতী উপনিবেশের কথা বলেছে। বণিকদের দেবতা মৈনা-মনসার নাম থেকেও এই নামের প্রচলন হওয়ার অসম্ভব নয়। ১০৫টি গ্রাম নিয়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়না পরগণা তৈরি হয় মুসলমান শাসনের শেষ দিকে। উৎকল শাসনকালে সবং, খা্ন্দার ও ময়না এই তিন পরগণার ভূভাগ ময়না চৌরার বা ‘চউরা’-র অন্তর্গত ছিল। [উৎকল ভাষায় চউরা শব্দের অর্থ দ্বীপাকার ভূমি ] রাজা তোডরমলের সময় এই তিন পরগণা ছিল একটি মাত্র পরগণার অন্তর্গত। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ময়না পরগণার গ্রামগুলিকে সবং ও তমলুক এই দুই থানায় ভাগ করা হয়। বর্তমানে সবং থানার অধীনে ৭টি গ্রাম, ময়না থানার অধীনে ৭১ টি গ্রাম, পিংলা থানার অধীনে ২০টি গ্রাম ও তমলুক থানার অধীনে ৭টি গ্রাম। প্রাচীন মানচিত্র ও পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দরের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল সমুদ্রমুখ (কানিংহাম)। কংসাবতী, কালীঘাই, বাকসী, ক্ষীরাই বা ক্ষীরাবতী এবং চন্ডী – এই পাঁচ নদী বিভিন্ন দিক থেকে এখানে এসে একত্রে মিলিত হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। সাধারণত এই ধরনের সঙ্গমস্থলকে সাধারণ ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় বসে মোহনা অথবা ‘মোয়ানা’। প্রাকৃতিক নিয়মে নদী যেখানে সমুদ্র মিশে যায়, স্রোতবাহিত মৃত্তিকা ও বালুকণা জমে সেখানে ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়। ক্রমে সমুদ্র মুখ সেখান থেকে দূরে সরে যায়। হতে পারে ‘মোয়ানা’ মুখে চর সৃষ্ট হয়েছিল বলে এই অ়্ঞ্চলকে ‘মোয়ানা’ চর বা ময়নাচর নামে ডাকা হত। সেচ বিভাগের কাগজে ময়নাচর deltoid tract বা চরভূমি এবং কালেক্টরীর কাগজে ময়নাচর নামে পরিচিত। পাল শাসন কালে ‘ময়না মন্ডল’ উৎকল শাসন কালে ‘চউরা’ এবং মুসলমান শাসন কালে ‘কিল্বা ময়না চৌরা’ নাম দেওয়া হয়েছিল।

উত্তর মুসলমান শাসন কালে উৎকলের অন্তর্গত হিজলীর অধীনে ময়না, সবং এবং খান্দার পরগণা বাহুবলীন্দ্র পরিবারের শাসনে ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কাল পর্যন্ত এই অঞ্চল তাদের শাসনে ছিল। ইংরেজ শাসনকালে অঞ্চলটি মেদিনীপুরের অন্তর্গত হয়ে থানায় বিভক্ত হয়।ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ময়না বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে আসে। পালবংশের একাদশ নরপতি দ্বিতীয় মহীপাল ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন হয়ে অনাধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃভূমি উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে সম্ভবত তিনিই দুর্গম নদীবেষ্টিত ভূখন্ডে ময়না জলদুর্গ স্থাপন করেন।ময়না দুর্গ বা ময়নাগড়ের সঙ্গে বৃহত্তর মোয়ানা চর বা ময়না চর বা ময়নার সম্ভাবত সরাসরি কোন যোগসূত্র ছিল না। সবিশেষ ময়নাগড়ের যে ভূখন্ড তার উৎপত্তি সম্ভবত দ্বীপের আকারে এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে। গড়ের পূর্ব দিকে কালনীগঙ্গা বা কংসাবতী আর অন্যান্য দিকে ছিল গভীর-অগভীর খাঁড়ি।ফলস্বরূপ স্থলসৈন্যের পক্ষে গড় আক্রমণ ছিল রীতিমত কঠিন।

ধর্মমঙ্গলে উল্লেখ আছে রাজা কর্ণসেন যখন ময়না এসেছিলেন, তিনি জলপথে কালিন্দী (কংসাবতীর শাখানদী) দিয়ে ময়নায় প্রবেশ করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল, ধর্মদেবতা, ধর্ম ঠাকুরের পুজা, রাজা কর্ণসেন, তাঁর পুত্র লাউসেন বা লবসেন এবং ময়না গড় এক কথায় সমার্থক। লোকশ্রুতি অনুসারে ময়না দুর্গ বা ময়নাগড় স্মরণাতীত কাল থেকে ধর্মের গড় নামেও পরিচিত। গড় ভূখন্ডের শেষ ভাগে আনুমানিক ৪থেকে ৫ কাঠা জমি লাউসেনের তক্ত নামে পরিচিত। বাহুবলীন্দ্র পরিবার আনুমানিক ৪ থেকে ৫ শতাব্দী এই গড়ে বাস করছেন। গড়ের বাইরে প্রথম ভুবলয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কিছু দিন আগে পর্যন্ত লাউসেনজিত ধর্মদেবতার মন্দির ছিল। মন্দির জরাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় বলে দেবতা এখন স্থানান্তরিত।লাউসেনের অন্যতম উপাস্যা ছিলেন রঙ্কিনী দেবি। বর্তমান লোকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশে রঙ্কিনী দেবির মন্দির ছিল। মন্দির ভগ্নপ্রায় হওয়ায় রঙ্কিনী দেবিও এখন মহাদেবের মন্দিরে স্থানান্তরিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব হলেও বাহুবলীন্দ্র পরিবার প্রাচীন দেব-দেবি বলে এখনও ধর্ম ও রঙ্কিনীর পুজো করেন। লাউসেনের রেশ ধরে ময়না একসময় ধর্মপুজোর অন্যতম কেন্দ্র ছিল।
দেশ
উৎপল কুমার বসু পুলিশ কমিশনারের কাছে ধমক খেয়েছিলেন

পুলিশ কমিশনারের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উৎপল কুমার বসু মহা ফাঁপরে পড়েছিলেন। রীতিমত ধমকে উঠেছিলেন দুঁদে পুলিশ কমিশনার পি কে সেন, ‘আপনি না কলেজের অধ্যাপক? ছেলে-ছোকরাদের ফিচলেমিতে কেন নিজেকে জড়ালেন?’ রীতিমত ধমকে উঠলেন দুঁদে পুলিশ কমিশনার পি কে সেন। ‘ছেলে-ছোকরারা অসামাজিক কাজ করেছে কি? ‘ছেলে-ছোকরারা অসামাজিক কাজ করেছে কি? তবে হ্যাঁ, এদের লেখাকে যেভাবে অশ্লীল এবং অসামাজিক বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে তা আমি মানতে রাজি নই।’ ধমকানির উত্তরে এমন স্পষ্ট ভাষণ শুনতে পুলিশ কমিশনার তৈরি ছিলেন না।
উৎপল কুমার বসু পুলিশ কমিশনারের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহা বিপত্তিতে পড়েছিলেন
তখন উনিশশো বাষট্টি সাল। সারা বাংলা জুড়ে এক অস্থির পরিস্থিতি। কথায় বলে, কবিরা সমাজ বদলাতে না পারলেও সমাজের প্রকৃত রূপকে লেখায় তুলে ধরতে পারে আর সেই থেকে নাকি সমাজ বদলায়। সমীর রায়চৌধুরি, মলয় রায়চৌধুরি, শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়রা তাঁদের লেখা দিয়ে ঠিক এই কাজটাই করছিলেন, যাকে সমালোচক-তাত্ত্বিকরা ‘হাংরি আন্দোলন’ বলে অভিহিত করেন। এই আন্দোলনটি না ছিল কোন সংগঠিত আন্দোলন, না তাতে নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং এর প্রকাশও ছিল বিক্ষিপ্ত।
আরও পড়ুনঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
জনৈক কবি সদ্য বিএ পাশ করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। হঠাৎ সুযোগ আসে জিওলজিতে অনার্স নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। সেই পড়ার সুবাদে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পা পড়ে চাইবাসায়। আড্ডা মারার লোভে একদিন হাজির হলেন সমীর রায়চৌধুরির বাড়ি। নিয়মিত এই আড্ডায় উপস্থিত হতে হতে ক্রমশ শক্তি-সুনীল, সন্দীপনের সঙ্গে তরুন কবিও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন।
এমএসসি পড়ার শেষে জুটল আশুতোষ কলেজে প্রভাষকের চাকরি। ওদিকে প্রশাসন তখন যে কোন উপায়ে ভাঙতে চাইছে আন্দোলন। পুলিশের কর্তারা বেছে বেছে কবি, সাহিত্যিকদের সদর দপ্তরে ডেকে এনে হেনস্থা করছেন। তার থেকে তরুণ কবিও বাদ গেলেন না। পুলিশি জুলুমের চাপে, আদালতে তাঁকে বলতে বাধ্য করানো হয় যে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কবি ও সাহিত্যিকরা অসামাজিক কর্মে লিপ্ত এবং তাঁরা অপরাধী।
সুনীল, শক্তি, মলয় রায়চৌধুরিদের সাথে সাথে উৎপল বসুও হাংরি আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন
প্রবল চাপের মুখে তরুণ কবি জবানবন্দী দিলেন, ‘আমি অবিবাহিত, আমার বয়স ২৮।১৯৬২ সন বা তার কাছাকাছি কোন এক সময়ে হাংরি পুস্তিকা আমার চোখে পড়ে। কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস এই আন্দেলনকারীদের আড্ডা মারার জায়গা। তাদের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে হাংরি পুস্তিকায় গদ্য ও কবিতা লিখেছি। কোথা থেকে ছাপানো হত আর কে তার খরচ যোগাত আমি জানি না। ১৯৬৪ সনে আমি কুসংস্কার নামে একটা লেখার পাণ্ডুলিপি দিই। তারপর আমি দু’ মাসের জন্য ডালহৌসী চলে যাই এবং কলকাতা ফিরে আমি আলোচ্য পুস্তিকাটি দেখতে পাই। পরে ডাকযোগে একটা কপি পেয়েছি। আমি মনে করি, তাদের সাহিত্য আন্দোলন নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে গেছে এবং আমি হাংরি আন্দেলন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছি।’
কলকাতায় কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে যখন এভাবে টানাহ্যাঁচড়া চলছে, তখন আমেরিকার বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে হাংরি আন্দেলন নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি তৈরি করেন এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কলেজের প্রভাষকের চাকরি থেকে তরুণ কবিকে নির্বাসিত হতে হয়।
‘পিয়া মন ভাবে’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন উৎপল কুমার বসু
কবি থাকেন তাঁর নিজের খেয়ালে। আছেন সব কিছুতে, আবার কোন কিছুতেই নেই। ঘুরে বেড়ান আপন মনে। লিখতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি বলেন, ‘মানুষের প্রবণতাই হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। সে তাই কবিতা লেখে। কবিতা লিখেই আত্মপ্রকাশের চর্চা করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের প্রবণতা না থাকলে হয়ত মানুষ আর কবিতা লিখবে না। কিন্তু আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা কি কোন দিন থেমে যেতে পারে?’
হাংরি আন্দোলন বাংলা ও সাহিত্যকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে বা আদৌ সমৃদ্ধ করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা এখনও চলতে পারে। তবে হাংরি আন্দোলন ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য, হোক না তা পুলিশের চাপে পড়ে, উৎপল কুমার বসুকে, সমালোচনা ও তিরস্কার, দুয়েরই আঘাত প্রবল ভাবে সইতে হয়েছিল। দু হাজার এগারো সালে সপ্তর্ষি থেকে প্রকাশিত ‘পিয়া মন ভাবে’ কাব্যগ্রন্থের জন্য দু হাজার চোদ্দ সালে কবিকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
দেশ
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে দেবী পক্ষের সূচনা হয়

‘মহালয়া’ একটি তিথি আর ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ একটি অনুষ্ঠান। দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা এবং বাঙালির আকাশে, এই তিথি আর অনুষ্ঠান এক সমার্থক রূপ ধরে আছে। মহালয়ার ভোরে তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শোনাও যেন বাঙালির অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি বলতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও মহালয়ার ভোর দিয়েই সূচনা হয় দেবীপক্ষের। তাঁর কণ্ঠের যাদুতে এখনও আপামর বাঙালি বিভোর হয়ে আছে।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও মহালয়ার ভোর দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালির জীবনে এটাই সমার্থক হয়ে আছে
স্ত্রী একবার স্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘স্তোত্রপাঠের সময়ে তোমার গলা ধরে আসে কেন?’ উত্তরে স্বামী বলেছিলেন, ‘মা চণ্ডীকে তখন সামনে দেখতে পাই আমি।’ অনেকেই বলেন,চণ্ডীপাঠের আগে তিনি নাকি স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে পুরোহিতের সাজে বসতেন। তবে তাঁর কন্যা বলেছেন, বাবাকে তিনি কখনও ঠাকুরকে একটি ধূপও দিতে দেখেননি।
আরও পড়ুনঃ বাংলা ও বাঙালির সব থেকে বড় আইকন মহানায়ক উত্তমকুমার
ঠাকুমা ভাল সংস্কৃত জানতেন। ঠাকুমার কাছেই সংস্কৃতের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র। প্রথম বার চণ্ডীপাঠ করেছিলেন দশ বছর বয়সে, রাজেন্দ্রনাথ দে’র বাড়িতে। অঙ্কে মন ছিল না। তবে স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। একবার এক প্রতিযোগিতায় ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ ছিল আবৃত্তির বিষয়। চল্লিশ পাতার কবিতা মুখস্থ করতে হবে অথচ প্রতিযোগিতার তিন-চার দিন আগে পর্যন্ত ছেলের কোন তাগিদ নেই। নির্দিষ্ট দিনে পৃষ্ঠা চারেক আবৃত্তি শুনে, বীরেন্দ্রকে থামিয়ে দেন, অতীব সন্তুষ্ট বিচারক। সেদিন প্রথম হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বীরেন্দ্র।
পরশুরামের ‘চিকিৎসা সঙ্কট’ নাটক পরিচালনা দিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বেতার জীবন শুরু
‘চিত্রা সংসদ’ নামে একটি ক্লাবে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ওরফে বাণীকুমার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সত্য দত্ত, বিজন বসু, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের সাথে বীরেন্দ্রও গান–বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি চর্চা করতেন। উনিশশো সাতাশ সালের ছাব্বিশে অগস্ট ডালহৌসির এক নম্বর গার্স্টিন প্লেসে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে বোম্বের ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। নতুন বেতারকেন্দ্রে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন মজুমদার। সহকারী রাইচাঁদ বড়াল ও রাজেন্দ্রনাথ সেন। তখন বাইরের দলও রেডিয়োয় অনুষ্ঠান করত। চিত্রা সংসদের সদস্যরা ঠিক করলেন, তাঁরাও বেতারে নাটক করবেন। পরশুরামের ‘চিকিৎসা সঙ্কট’-এর নাট্যরূপ নিয়ে বীরেন্দ্র হাজির হলেন নৃপেনবাবুর সামনে। উনিশশো আঠাশ সালের একুশে অগস্ট বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনায় পরিবেশিত হল সেই নাটক।
বিএ পাশ করে চাকরি নিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসে। সময় পেলে চলে আসতেন রেডিয়ো অফিসে। শেষে রেলের চাকরি ছেড়ে বেতারের চাকরিতে যোগ দিলেন। কিছুদিন পরে আত্মপ্রকাশ হল ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার। সাল উনিশশো ছত্রিশ জানুয়ারি ২৫, পত্রিকা প্রকাশের চার দিন আগে মারা গেলেন পঞ্চম জর্জ। সম্পাদকের ইচ্ছে পত্রিকা প্রকাশ করবেন পঞ্চম জর্জ সংখ্যা রূপে। দায়িত্ব পড়ল বীরেন্দ্রর ওপর। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে জর্জকে নিয়ে লেখা বইপত্তর জোগাড় করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন বীরেন্দ্র। নির্দিষ্ট সময়ে বেতার জগৎ প্রকাশিত হয়।
উনিশশো বত্রিশের ষষ্ঠীর ভোরে বেতারে প্রথম প্রচারিত হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ গ্রন্থনা ও শ্লোক আবৃত্তিতে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
উনিশশো বত্রিশের ষষ্ঠীর ভোরে বেতারে প্রথম প্রচারিত হয়কালজয়ী অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী।’ গানে পঙ্কজ মল্লিক আর গ্রন্থনা ও শ্লোক আবৃত্তিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানের আগের রাতে আটটা–ন’টা নাগাদ শতরঞ্চি আর বালিশ নিয়ে চলে গেলেন বেতারকেন্দ্রে। কায়স্থ ঘরের ছেলে চণ্ডীপাঠ করবে, ভয় পেয়েছিলেন বেতার কর্তৃপক্ষ। তবে বাণীকুমার বলেছিলেন, ‘এটা শুধু বীরেনই করতে পারে, ও-ই করবে।’ অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলে উঠলেন, ‘‘আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর…’’ পঙ্কজ মল্লিক হাত নেড়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন, ‘ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।’ সেই শুরু…এখনও চলছে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। সমগ্র বিশ্বের আর কোন বেতার কেন্দ্রে বিরামহীন এত বছর ধরে চলতে থাকা অনুষ্ঠানের এমন উদাহরণ আর একটিও নেই।
দেশ
বিদ্যাসাগরকে সম্মান দিতে বাংলা চূড়ান্ত ব্যর্থ

জন্ম: সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০
বীরসিংহ, বাংলা, ব্রিটিশ ভারত
মৃত্যু: জুলাই ২৯, ১৮৯১
জীবন সঙ্গী: দীনময়ী দেবী
সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর সহপাঠীর কাছে শঠতার শিকার হয়েছিলেন
সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক জন মিয়র প্রতিযোগিতা আয়োজন করলেন পদার্থবিদ্যা বিষয়ে একশত সংস্কৃত শ্লোক লেখার। এক সহপাঠী ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রস্তাব দিলেন, দু’জনে পঞ্চাশটি করে শ্লোক লিখে পুরস্কারের অর্থ ভাগাভাগি করে নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে সহপাঠী জানালেন, তার অংশের পঞ্চাশটি শ্লোক সে লিখতে পারেনি। তাই শুনে বিদ্যাসাগর নিজের লেখা পঞ্চাশটি শ্লোক ছিঁড়ে ফেললেন। ঈশ্বরচন্দ্র পরে জানতে পেরেছিলেন, সহপাঠী ছাত্রটি পুরো একশত শ্লোকই জমা দিয়েছে। ধূর্ত সহপাঠীর অভিপ্রায় বুঝতে ঈশ্বরের আর বাকি থাকল না। বিদ্যাসাগর পরের বছর অবশ্য পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন।
সারা জীবনে বিদ্যাসাগরকে এরকম ঘটনার মুখোমুখি খুুব একটা কম হতে হয়নি। সমাজ, পরিজন,পরিবারের থেকে আজীবন আঘাত পেয়েছেন। সাত ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই কম বয়সে মারা যায়। পিতা ঠাকুরদাস ঠিক করেছিলেন, কলকাতা ছেড়ে কাশী বাস করবেন। বড় ছেলে ঈশ্বরের অনুরোধে মত পালটে সিদ্ধান্ত নিলেন বীরসিংহ ফিরে যাবেন। ছোট ভাই ঈশানচন্দ্র মত দিলেন, দেশে ফিরে সংসারী থাকার পরিবর্তে বাবার উচিত কাশী যাওয়া। যারপরনাই বিড়ম্বনায় পড়ে ঠাকুরদাস শেষে কাশী গেলেন। বাবার যাতে কাশীবাসে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিদ্যাসাগর প্রায়ই কাশী যেতেন। জীবনভর এ কর্তব্য তিনি পালন করেছেন।
জীবনভর বিদ্য়াসাগর আত্মীয় পরিবার সবাইয়ের থেকে আঘাত পেয়েছেন
‘সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরির‘ অধিকারের দাবিতে অগ্রজের সঙ্গে দীনবন্ধুর বিবাদ, আদালতে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যদিও শেষে তার নিষ্পত্তি হয় সালিশির মাধ্যমে। ভাই অন্যায্য দাবি করলেও দাদা কি পিছিয়ে থাকতে পারে! গোপনে দীনবন্ধুর স্ত্রীর হাতে টাকা দিয়ে আসতেন বিদ্যাসাগর। যদিও এক সময় বিষয়টি আর গোপন ছিল না।
আরও পড়ুন: কি আশ্চর্য! বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হুবহু নকল
দাদাকে অপমান করতে আর এক ভাই শম্ভুচন্দ্রও কম ছিলেন না। ক্ষীরপাইয়ের কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশীগঞ্জের মনোমোহিনী দেবীর বিধবা বিবাহ থেকে, যে কোনও এক কারণে বিদ্যাসাগর নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিধবা বিবাহের সূত্রপাত যাঁর হাতে, অগ্রজ সেই বিদ্যাসাগরকেই, শম্ভুচন্দ্র ‘কাপুরুষ‘ বলে দোষ দিয়েছিলেন। ভাই বলেই হয়ত এমন সাহস দেখাতে পেরেছিল, নাহলে বিদ্যাসাগরের ঘোর বিরোধিদের মধ্যেও কেউ কোন দিন এমন সাহস দেখাননি।
জীবনে তিনি সব থেকে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন পুত্র নারায়ণচন্দ্রের থেকে। পুত্রের কাজকর্মে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে রীতিমত লিখিত আকারে ছেলের সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ,সেজো মেয়ে বিনোদিনীর স্বামী সূর্যকুমার অধিকারী, হিসাবের গরমিলের দায়ে ধরা পড়েছিলেন বিদ্যাসাগরের হাতে। সদুত্তর না দিতে পারায়, বিদ্যাসাগর তাঁকে অপসাহিত করে, বৈদ্যনাথ বসুকে নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।
বিদ্যাসাগর সমাজের প্রকৃত অবস্থান বুঝতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন
স্ত্রী দিনময়ী দেবীর পক্ষেও এত বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কার্যত অসম্ভব ছিল। অনেক গবেষক যদিও এ নিয়ে বিদ্যাসাগরকেই দায়ী করেছেন, তবে বাস্তবে দেখা যায় স্ত্রীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর তাঁর ইচ্ছেপূরণের চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর হাত ধরে, ছেলেকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য মায়ের প্রার্থনা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।
সতীদাহ রুখে দিয়ে রামমোহন যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, তার পরিসমাপ্তির দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আইন পাশের পরে, কালীমতী দেবীর সাথে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের আইনসম্মত বিধবা বিবাহে রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদের ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি তাঁকে সমাজের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে বোধোদয় করিয়েছিল। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই বাংলা যে তাঁকে বুঝতে ও যোগ্য সম্মান দিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ, তার সূচনা সম্ভবত সেদিনই রচিত হয়েছিল।


